ড. ইউনূসের তিন শূন্য তত্ত্ব ও বাস্তবতা
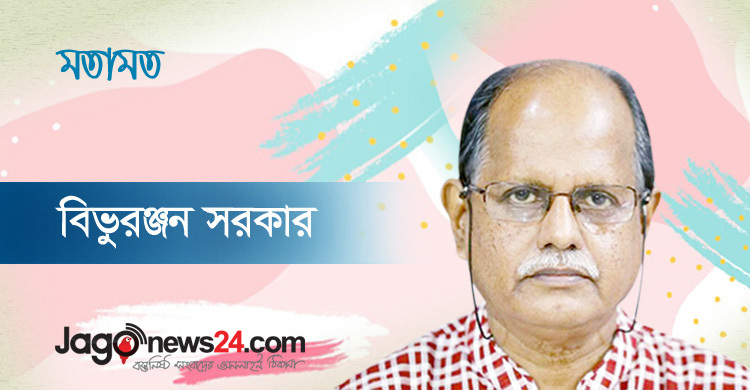 সাংবাদিক ও কলামিস্ট বিভুরঞ্জন সরকার
সাংবাদিক ও কলামিস্ট বিভুরঞ্জন সরকার
ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নাম উচ্চারণ করলেই চোখের সামনে ক্ষুদ্রঋণের সেই প্রাথমিক উচ্ছ্বাস আর জাতিসংঘের মিলনায়তনে নোবেল পদকের গর্বিত মুহূর্ত ভেসে ওঠে; একই সঙ্গে ভেসে ওঠে বিতর্ক, দোলাচল, প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহের টুকরো ছায়া। ক্ষুদ্রঋণের সাফল্য আর ব্যর্থতার কাহিনি লতাপাতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অজস্র গ্রামে—কিছু জায়গায় তা স্বনিযুক্তির আলো জ্বেলেছে, আবার কোথাও মানুষকে ফেলে দিয়েছে ঋণের দুষ্টচক্রে।
আজ, যখন তিনি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মঞ্চে, তাঁর নতুন স্বপ্ন ‘থ্রি জিরো’—দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও কার্বন নির্গমনকে শূন্যে নামিয়ে আনা—দেশের নীতি ও আন্তর্জাতিক আলোচনামঞ্চে জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু এই বিপুল আকাঙ্ক্ষার অভীষ্টে পৌঁছাতে গেলে প্রশ্নগুলোও সমান জোরে ধাক্কা দেয়: এটা কি উদার মানবিকতার বাস্তব নকশা, নাকি এক ধরনের মধুর ইউটোপিয়া, যার নেপথ্যে রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা আর বৈশ্বিক ইমেজ পলিশের কৌশল লুকিয়ে আছে?
দারিদ্র্য শূন্যের কথা বলতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে সেই আশ্চর্য পরিসংখ্যান—বিশ্বব্যাংকের হিসাবে ১৯৯০ থেকে ২০১৯ মাঝে চরম দারিদ্র্যের হার ৩৬ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯ শতাংশে, যার পেছনে চীনের শিল্পায়ন ও দক্ষিণ এশিয়ার শ্রমবাজার ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু একই গ্রাফে দেখা যায়, বৈষম্যের ফারাকটা একই সময়ে ফেঁপেছে—ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি ল্যাবের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলে ধনী-দরিদ্রের আয়ের ব্যবধান এখনো ঊর্ধ্বমুখী। ইউনূসের ক্ষুদ্রঋণ মডেল গ্রামীণ নারীদের হাতে সীমিত পুঁজি তুলে দিলেও ঋণের সুদহার, প্রশিক্ষণের অভাব, বাজারসুবিধার সংকট অনেক ক্ষেত্রেই লাভকে খেয়ে ফেলেছে।
ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে ২০১০ সালে সুদের কিস্তি শোধে ব্যর্থ হয়ে ধারাবাহিক আত্মহত্যার ঘটনা বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল: ক্ষুদ্রঋণ কি দারিদ্র্য দূর করছে, নাকি নতুন ধার- দেনার দানব সৃষ্টি করছে? বাংলাদেশেও একাধিক এনজিও মাঠপর্যায়ে গ্রামের সহজ-সরল মানুষকে চাপে ফেলেছে—পূর্বশর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে দেনার দায়ে গবাদি পশু পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সুতরাং দারিদ্র্য শূন্যের সোনালি সোপান তৈরির আগে ঋণপ্রাপ্তির পাশাপাশি ন্যায্য বাজারদর, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, সামাজিক নিরাপত্তা—এই সমন্বিত অবকাঠামো গড়ে তোলা জরুরি; নইলে ‘শূন্য’ শব্দটা পোস্টারেই চকচক করবে, বাস্তবের মাটিতে বসন্ত নয়, বরং হতাশার ধূলিঝড়ই ছড়াবে।
ড. ইউনূসের অতুলনীয় কথার জাদু যেমন অনুপ্রাণিত করে, একইসঙ্গে তাঁর তত্ত্বের ত্রুটিবিচ্যুতি বিশ্লেষণও প্রয়োজনীয়। কারণ বৈশ্বিক নায়কত্ব মানে শুধুই ফুটপাতের ফুল ছুড়ে দেওয়া নয়, মাঝেমাঝে কাঁকর-ইটের ক্রিটিক্যাল পথে হাঁটাও—যাতে স্লোগানের আগুনে দাবদাহ না বাড়ে, বরং নৈতিকতার আলো ছড়ায়।
তারপর আসে বেকারত্ব শূন্যের প্রশ্ন, যেখানে ইউনূসের পপুলার মন্ত্র—‘সবাই উদ্যোক্তা’—শুনতে যতই অনুপ্রেরণাময় হোক, বাস্তবে তা অনেকের কাছেই গোলাপি কাচের চশমা পরে ভবিষ্যৎ দেখার শামিল। গ্লোবাল এমপ্লয়মেন্ট ট্রেন্ডস-এর তথ্য বলছে, কোভিড-পরবর্তী বিশ্বে অন্তত ১৭ কোটি মানুষ স্থায়ী আয়হীন, ননফরমাল খাত-নির্ভর জীবিকা খুঁজছে; এর মধ্যে অনেকে মাঝবয়সী, প্রযুক্তি-অজ্ঞ বা স্বল্পশিক্ষিত—উদ্যোক্তা হওয়ার ঝুঁকি নেওয়ার অর্থ তাদের কাছে পেটের ভাতের শেষ মুঠোটুকু বাজি ধরা। অ্যান্ট্রেপ্রেনারশিপ পরামর্শদাতা রবার্ট রাইখ সাবধান করেছেন: ‘প্রত্যেককে উদ্যোক্তা বানানোর স্বপ্নে যে ঝুঁকি-সন্তুলন লাগে, তা নেই উন্নয়নশীল দেশের সিংহভাগ মানুষের ঝুলিতে।’
ধরা যাক, বাংলাদেশে প্রতিবছর কর্মবাজারে যুক্ত হয় প্রায় ২২ লক্ষ তরুণ; তার মধ্যে কারিগরি তথা ভোকেশনাল শিক্ষা পায় সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ। অবশিষ্ট ৮০ শতাংশ যদি স্বনিযুক্তি করতে চায়, তবে শুধু ক্ষুদ্রঋণ নয়, লাগবে আধুনিক সরঞ্জাম, মার্কেট লিংকেজ, বিপণন প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল স্কিল, ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম—এগুলোর কোনোটিই এখনো গণহারে সহজলভ্য নয়। উপরন্তু, প্রযুক্তিগত অটোমেশন বিপুল হারে ‘রুটিন’ কাজ হারিয়ে দিচ্ছে—২০২৪ সালে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের রিপোর্ট বলছে, জেনারেটিভ এআই অন্তত ৮ কোটি চাকরি পুনর্গঠন বা বিলুপ্তির ঝুঁকিতে ফেলে দিয়েছে। এই বাস্তবতায় ‘বেকারত্ব শূন্য’ উচ্চারণ করতে হলে রাষ্ট্রকে কেবল তত্ত্ব প্রচার নয়, শিল্প পুনর্গঠন, উচ্চ-মূল্যভিত্তিক কৃষি, গ্রিন-টেক, তথ্যপ্রযুক্তি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে গণ- প্রশিক্ষণ—এই সম্পূর্ণ ইকোসিস্টেম দাঁড় করাতে হবে; না হলে উদ্যোক্তা- স্বপ্ন হবে নদীর বালুচরের ঘর—দৃষ্টিনন্দন হলেও প্রথম জোয়ারেই বিলীন।
সবশেষে আসে কার্বন নির্গমন শূন্য, যেখানে ইউনূসের অবস্থান নৈতিকভাবে দৃঢ়, কিন্তু রূঢ় অর্থনীতির মুখোমুখি হয়ে পড়লে সেই দৃঢ়তা তীব্র আলো-ছায়া ফেলে। ইউরোপিয়ান গ্রিন ডিল বা যুক্তরাষ্ট্রের ইনফ্লেশন রিডাকশন অ্যাক্ট নিয়ে পশ্চিমা দুনিয়া কার্বন নির্গমন কমাতে ট্রিলিয়ন-ডলার বিনিয়োগ করছে, অথচ একই সময়ে গ্লোবাল সাউথে উন্নয়নমূলক অবকাঠামো ও কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাড়ছে, কারণ সস্তা জ্বালানি ছাড়া উৎপাদন খরচ সামাল দেওয়া কঠিন।
বাংলাদেশ নিজেই ২০৪১ সাল পর্যন্ত শিল্পায়নের লক্ষ্য ধরে বছরে ৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি চায়—স্বল্পকালীন প্রবৃদ্ধির ক্ষুধা আর দীর্ঘকালীন জলবায়ু নীতির বিরোধ বাঁধবেই। আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল দ্রুত ছাড় না দিলে দক্ষিণ এশিয়ার অনেক রাষ্ট্র তারস্বরে ‘গ্রিন’ স্লোগান দেবে, অথচ কয়লার ধোঁয়া বুকে টেনে কারখানার চিমনিতে কালো ধূম্রলেখা বাড়াবে! উপরন্তু, কার্বন শূন্য অর্থনীতি গড়ে তুলতে চাইলে নবায়নযোগ্য শক্তির প্রযুক্তি- নির্ভরতা, গ্রিড আধুনিকায়ন, বিদ্যুৎ সংরক্ষণব্যবস্থা—এসব বিনিয়োগ বিশাল; এগুলোর তহবিল, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর নিশ্চিতে উন্নত-দরিদ্র দেশের আস্থার ব্যবধান ভাঙতে না পারলে ‘নেট জিরো’র স্লোগান উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষয়িষ্ণু মাটির মতো ভেঙে ভেঙে পড়বে। এ অবস্থায় একজন রাষ্ট্রনায়ক ইউনূসের উচিত হবে স্বপ্নের সঙ্গে খরচপত্রের খাতা খোলা, ন্যায্য রূপান্তর-ভিত্তিক (Just Transition) ফান্ড দাবি করে গ্লোবাল সাউথের জোট গড়ে তোলা; নইলে শূন্য নির্গমন শুধু আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাইক্রোফোনেই গমগম করবে, ভাটার কালে দুর্ভোগ বাড়িয়ে দেবে উপকূল, হাওর, মরুভূমির দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য।
এই তিনটি ‘শূন্য’ লক্ষ্য যখন একই সরলরেখায় বসে, তখন আরেকটি মৌল সমস্যা সামনে আসে—ব্যক্তিনির্ভর এনজিও-ভিত্তিক উদ্যোগ বনাম প্রাতিষ্ঠানিক রাষ্ট্রযন্ত্রের বাস্তবতা। ক্ষুদ্রঋণ যুগে ইউনূস ছিলেন মূলধারার ব্যাংকিংয়ের বাইরে এক বিকল্প সত্তা; তাঁর ব্যক্তিগত খ্যাতি অনেক বাধা টপকে গ্রামীণ মডেল প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু সরকারপ্রধান ইউনূসের অবস্থান অন্যতর—এখন তাঁর প্রতিটি ঘোষণায় বাজেট, আইন, পার্লামেন্ট, বিরোধী দল, নাগরিক সমাজ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গাঁথা।
অতএব, নীতির সাফল্য-ব্যর্থতা আর শুধু তাঁর কৃতিত্ব-দায় নয়, পুরো প্রশাসনের সমষ্টিগত জবাবদিহি। সমালোচকেরা ঠিক তাই প্রশ্ন তোলেন: ‘থ্রি জিরো’ কি আদতে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মডিউল নাকি এক ব্যক্তির বৈশ্বিক ব্র্যান্ড? রাষ্ট্রনীতি যদি ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ক্যাম্পেইনে পর্যবসিত হয়, তবে তা স্থায়িত্ব হারায়; যেমন আফ্রিকার কিছু দেশে দেখা গেছে—একজন প্রভাবশালী নেতা বিদায় নিতেই তাঁর দাতব্য ভাবনা-কেন্দ্রীক কর্মসূচি মুখ থুবড়ে পড়েছে।
রাষ্ট্রশক্তিকে এড়িয়ে ‘সামাজিক ব্যবসা’ দিয়ে কল্যাণ নিশ্চিত করার যে ধারণা ইউনূস বহু বছর ধরে তুলে ধরেছেন, তা তাত্ত্বিকভাবে আকর্ষক হলেও বাস্তবে পুঁজিবাদের ভেতর বসে লড়াই করে; কারণ ‘লাভের বিনিময়ে কল্যাণ’ ধারা বাজারে প্রতিযোগিতায় পড়লে অনেক সময় প্রান্তিক মানুষের স্বার্থকেই আবার দুই নম্বর সিটে বসায়। উদাহরণস্বরূপ, মেক্সিকোতে কিছু সামাজিক ব্যবসা কল সেন্টার চালু করেছিল যেখানে লাভ সীমিত রাখা হয়েছিল, কিন্তু কর্পোরেট জায়ান্টরা উচ্চ-মূল্যে আউটসোর্সিং নিয়ে আসায় ক্ষুদ্র ধাঁচের এ উদ্যোগ বাজার হারিয়ে ফেলে; কর্মীরা আবার চাকরি হারায়। কাজেই সামাজিক ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখতে হলে রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ, ভর্তুকি, নীতিসমর্থন দিতে হয়—যা আবার ‘ব্যবসা বনাম সরকার’ দ্বন্দ্বকেই ঘুরেফিরে হাজির করে।
সমালোচনা সেখানে আরও গাঢ় হয়, যখন ক্ষুদ্রঋণের অন্ধকার দিক উঠে আসে। বাংলাদেশ, নেপাল, কঙ্গো, কসোভো—বিভিন্ন স্থানে মাঠজরিপ বলছে, ঋণখেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার ভয়ে অনেকে আরও বেশি ঋণ তুলে কিস্তি শোধে নামে, ফলে নতুন কিস্তির বেড়ি পড়ে পায়ের শেকল আরও শক্ত হয়; নারীরা নিজেদের গয়না বা বাসনের থালা বিক্রি করে কিস্তি মেটায়, পরিণামে ঘরের খাবার কমে, শিশুর পুষ্টিহীনতা বাড়ে। তবুও মাঠকর্মীরা পুনঃঋণ দিতেই আগ্রহী, কারণ সাফল্যের সূচকে ‘ঋণপ্রদানের অঙ্ক’ই বড়ো হয়ে দেখা যায়, গ্রাহকের দীর্ঘমেয়াদি স্বনির্ভরতা নয়। ক্ষুদ্রঋণ-ইন্ডাস্ট্রির প্রায় তিন দশকের অভিজ্ঞতা শিক্ষা দেয়—ঋণ দিলেই ‘দারিদ্র্য হারিয়ে যাচ্ছে’ বাণী যতটা আবেগতাড়িত, বাস্তবে ততটাই অসম্পূর্ণ।
প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি ‘থ্রি জিরো’ একেবারেই অলীক? উত্তর তত সহজ নয়। মানবসভ্যতার ইতিহাস বলে, শতবছর আগে রাইট ভাইয়ের বিমান আকাশ ছুঁতেই মানুষ হেসেছিল, আর আজ হাজার কোটি ডলার খরচ করে মঙ্গলে বসতি গড়ার কথা ভাবছে। সুতরাং উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন অমূল্য; তবে স্বপ্নের মানচিত্রকে যদি ভূমি জরিপের মত কদর না দেওয়া হয়, তবে পথ স্পষ্ট হয় না। ইউনূসের এই উচ্চাশাফুলকে মাটিতে রোপণের প্রাথমিক শর্ত—টেকসই, তথ্যনির্ভর, অংশগ্রহণমূলক নীতি। অর্থাৎ তাকে স্বীকার করতে হবে—দারিদ্র্যের সমাধান শুধু ঋণপ্রস্তাব নয়, আয়কর নির্ভর প্রগতিশীল রাজস্বনীতি, ভূমি সংস্কার, গুণগত শিক্ষা, সর্বজনস্বাস্থ্য, নারীর সম্পত্তির অধিকার—এসবের সমষ্টি। বেকারত্ব কমাতে অধুনা ‘ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম’, ‘স্কিল-৬০’ বা ‘লাইফ-লং লার্নিং অ্যাকাউন্ট’-এর মত ধারণা বিবেচনায় নিতে হবে। কার্বন জিরোতে যেতে হবে ধাপে ধাপে—২০৩০ সালের মধ্যে কয়লা নির্ভরতা অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে, ২০৪০ এর মধ্যে গ্রিড-স্টোরেজ বাড়িয়ে নবায়নযোগ্য শক্তি ৫০ শতাংশে তুলতে হবে; এ পথচিত্র অবশ্যই খরচ, প্রয়োজন, বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে করে সাজাতে হবে।
রাজনীতির বাস্তবতায় আরেকটি চ্যালেঞ্জ উঁকি দেয়—কোনো সরকারপ্রধানের মেয়াদ সীমিত, অথচ ‘থ্রি জিরো’ প্রকল্প বহুবছরের। তাই দলমত নির্বিশেষে জাতীয় ঐকমত্য গড়া অপরিহার্য, যাতে ক্ষমতার পালাবদলে স্বপ্নের চাকায় আরেক দফা ঘুরপাকে না পড়ে। জার্মানির এনার্জি-বেন্ডে বা ডেনমার্কের ‘সিরোসিম’ কৌশল দেখায়—দলবদল হলেও কার্বন নীতিতে গভীর ভিত্তি অক্ষুণ্ন থাকে, কারণ সামাজিক-রাজনৈতিক সব পক্ষই নীতির মালিকানা নেয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, যেখানে রাজনৈতিক মেরুকরণ প্রবল, সেখানে ‘থ্রি জিরো’কে ব্যক্তির আসন থেকে টেনে নামিয়ে রাষ্ট্রের টেবিলে বসাতে হবে; সংসদীয় পর্যালোচনা, সুশাসন সূচক, বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা—এগুলো দিয়ে জবাবদিহি নিশ্চিত হলে তবেই দশকব্যাপী প্রকল্পে ধারাবাহিকতা থাকবে।
সুতরাং লেখাটি যদি কারও কানে ‘তেল মারার’ মতো শোনায়, তবে সে শোনার দায়ও আংশিক পাঠকের; আবার লেখকের দায় আরও বেশি—শ্লাঘার আড়ালে গোপন জিজ্ঞাসা, সম্ভাবনার পাশে সন্দেহ, জয়গানের ফাঁকে খোলা সমালোচনা—এগুলো লিখতে না পারলে লেখা একপেশে তোষামোদে পরিণত হয়। ইউনূসের অতুলনীয় কথার জাদু যেমন অনুপ্রাণিত করে, একইসঙ্গে তাঁর তত্ত্বের ত্রুটিবিচ্যুতি বিশ্লেষণও প্রয়োজনীয়। কারণ বৈশ্বিক নায়কত্ব মানে শুধুই ফুটপাতের ফুল ছুড়ে দেওয়া নয়, মাঝেমাঝে কাঁকর-ইটের ক্রিটিক্যাল পথে হাঁটাও—যাতে স্লোগানের আগুনে দাবদাহ না বাড়ে, বরং নৈতিকতার আলো ছড়ায়।
পথ যত দুর্গম হোক, স্বপ্নহীন মানুষ সভ্যতা গড়তে পারে না; আবার স্বপ্নের সিঁড়ি যদি মাটি থেকে খুঁটির জোর না পায়, তবে তা ভেঙে পড়ে। ইউনূসের ‘থ্রি জিরো’ সেই স্বপ্ন-সিঁড়ি—এখন দেখে নিতে হবে, এর বাঁশ কতটা পোকামারা-মুক্ত, দড়ির গিঁট কতটা পোক্ত, আর সিঁড়ির নিচে জমিন কতটা সমতল। পরীক্ষার ফলাফল দেবে সময়, দেবে মানুষ, দেবে প্রকৃতি। তবে প্রশ্ন করা, তর্ক করা, পরিমাপ করা—এই বুদ্ধিবৃত্তিক দায় এড়িয়ে লিখতে গেলে যতই সুখপাঠ্য হোক, পাঠকের চোখ তেলের দীপ্তি টের পেতেই পারে। তাই, সমালোচনার লণ্ঠন হাতে রেখেই যদি আমরা ইউনূসের স্বপ্নের পথ ধরে এগোই, তবে প্রত্যাশা আর বাস্তবতার মেলবন্ধন হয়তো একদিন সত্যিই ‘তিন শূন্য’কে সংখ্যাতত্ত্ব নয়, মাটির বাস্তবতায় রূপ দেবে; আর যদি না দেয়, অন্তত ইতিহাস জানবে—সমালোচকেরা সে দিন প্রশ্ন তুলেছিল, আর সেটাই ছিল গণতন্ত্রের অক্সিজেন, উন্নয়নের জিডিপি, মানবতার অফুরান প্রাণশক্তি।
লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক, কলামিস্ট।
এইচআর/এএসএম



