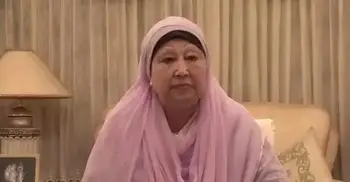করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এবং বাস্তবতা

ডা. শাহীন আক্তার
আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) এবং সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) যৌথ গবেষণায় ঢাকার প্রায় অর্ধেক মানুষের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার যে চিত্র উঠে এসেছে সেটি দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য ঝুঁকির বার্তা দিচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।
সরকারের আইইডিসিআর ও আন্তর্জাতিক সংস্থা আইসিডিডিআর,বি’র যৌথ গবেষণায় ঢাকার ৪৫ শতাংশ মানুষের দেহে করোনাভাইরাসের অ্যান্টিবডি পাওয়া গেছে বলা হয়েছে। তার মানে, এই ৪৫ শতাংশ মানুষ কখনও না কখনও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। সুতরাং এই হারের ওপর ভিত্তি করে বলা হচ্ছে যে, ঢাকায় ইতোমধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় এক কোটি মানুষ। রাজধানীর বস্তি এলাকায় সংক্রমণের হার আরও বেশি অর্থাৎ ৭৪ শতাংশ।
কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে সংক্রমণের যে তথ্য প্রচার করা হচ্ছে, তাতে ঢাকায় এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা দুই লাখেরও কম। এখান থেকেই প্রশ্ন আসে, তাহলে সরকারের প্রচারিত তথ্য কতটুকু যুক্তিযুক্ত! এই হিসাব যদি শুধু ঢাকার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তাহলে সারাদেশে করোনা সংক্রমণের সরকারি যে হিসাব দেয়া হয়েছে, সেটির সঙ্গে বাস্তবে করোনা সংক্রমণের হার কতটুকু তারতম্য হতে পারে, আর সরকারের প্রচারিত তথ্যের সঙ্গে গবেষণার ফলাফলের এত পার্থক্যই বা কেন? যদিও সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ গবেষণার নমুনার সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

গবেষণাটি যেভাবে পরিচালনা করা হয় এবং এর সীমাবদ্ধতা
গবেষণার জন্য ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ১২৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ২৫টি ওয়ার্ড ও আটটি বস্তি বেছে নেয়া হয়। মোট ৩,২২৭ টি খানা থেকে ১২,৬৯৯ জনকে জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গবেষণার (আরটিপিসিআর ও অ্যান্টিবডি) নমুনা সংগ্রহ করা হয় মধ্য এপ্রিল থেকে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত। মোট ১২,৬৯৯টি নমুনা প্রথমে আরটিপিসিআর পরীক্ষা করে ৯.৮% মানুষের শরীরে করোনার উপস্থিতি পাওয়া যায় অর্থাৎ যে সময়কালে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল তখন ৯.৮% মানুষ করোনায় আক্রান্ত ছিলেন।
গবেষণায় আরও বলা হয়, ৮২% উপসর্গ ও লক্ষণহীন করোনায় আক্রান্ত ছিলেন এবং ১৮% লক্ষণ ও উপসর্গযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে যাদের শরীরে করোনার উপস্থিতি পাওয়া যায় তাদের করোনার লক্ষণ ও উপসর্গযুক্ত এবং লক্ষণ ও উপসর্গ নেই এমন দুই দলে ভাগ করে মোট ৮১৭ জনের (শহরের ৬৯২ জন এবং বস্তির ১২৫ জন) অ্যান্টিবডি টেস্ট করা হয়। টেস্টের ফলাফলের ভিত্তিতে ঢাকা শহরের ৪৫% এবং বস্তিতে ৭৪% মানুষের শরীরে করোনার অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়। যদিও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গবেষণার সীমাবদ্ধতার কারণে প্রাপ্ত ফলাফলটি গ্রহণযোগ্য নয় এবং ভবিষ্যতে প্রতিনিধিত্বমূলক সংখ্যক নমুনা সংগ্রহ করে আরও বড় পরিসরে গবেষণা করতে হবে।

রক্তের নমুনার সংখ্যা কত হলে তা ঢাকা মহানগরীর প্রতিনিধিত্ব করবে— এমন প্রশ্নের উত্তরে আইইডিসিআরের পরিচালক অধ্যাপক তাহমিনা শিরীন প্রথম আলোকে বলেছিলেন, ‘প্রতিনিধিত্বমূলক হওয়ার জন্য কমপক্ষে তিন হাজার ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষা দরকার। পরীক্ষা হয়েছে ৮১৭ জনের।’[১]
[১. ‘রাত ১১টায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল গবেষণার সীমাবদ্ধতা’, ১৪ অক্টোবর ২০২০, প্রথম আলো]
আইইডিসিআরের পরামর্শক ডা. মুস্তাক হোসেন বলেন, ‘অ্যান্টিবডি টেস্টের জন্য ৯.৮% করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির প্রত্যেকের স্যাম্পল যদি পাওয়া যেত তাহলে বলা যেত এখন পর্যন্ত ঢাকা শহরে যত মানুষ আক্রান্ত হয়েছে তাদের সংখ্যাটা বা তাদের সংক্রমণের হার আসলে কত। অ্যান্টিবডি টেস্টে সমস্ত রোগীর ধারণা পাওয়া যায়। আর আরটিপিসিআরে ওই মুহূর্তে কতজন আক্রান্ত হয়েছে সেটা পাওয়া যায়। মার্চ মাসের রোগী তো জুলাই মাসে আরটিপিসিআর করে পাওয়া যাবে না। মার্চ মাসে রোগী আক্রান্ত হয়েছে কিনা, সেটা জুলাই বা আগস্টে অ্যান্টিবডি টেস্ট করে পাওয়া যাবে। এই গবেষণায় ১২ হাজারের কিছু বেশি আরটিপিসিআর করা হয়েছে কিন্তু এর সমপরিমাণ যদি অ্যান্টিবডি টেস্ট করা হতো তাহলে এটা তুলনামূলক হতো। সুতরাং মাত্র ৬৯২টি স্যাম্পল পরীক্ষা করে পুরো ঢাকার চিত্র পাওয়া সম্ভব নায়। আবার বস্তির স্যাম্পল তো আরো কম, মাত্র ১২৫টি। সেটিও প্রতিনিধিত্বমূলক নয়। গবেষণাটি আরও বড় আকারে করা প্রয়োজন। জেলা পর্যায়ে ৩২ জেলার মধ্যে ৩১টি জেলার তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি ইতোমধ্যে। সবগুলোর ফলাফল একসঙ্গে নিয়ে আসলে আমরা হয়তো প্রকৃত একটা চিত্র পেতে পারি।’
করোনা সংক্রমণের সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউয়ের কথা যখন বলা হচ্ছে সেই মুহূর্তে এই গবেষণা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গবেষণার সঙ্গে জড়িতরা বলেছেন, আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে তারা এই গবেষণা করেছেন। কিন্তু গবেষণায় নমুনার সংখ্যা নিয়ে সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ প্রশ্ন তুলেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন, ‘গবেষণার পদ্ধতি নিয়ে তাদের কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মাত্র ৬৯২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৪৫ শতাংশের অ্যান্টিবডির যে তথ্য পাওয়া গেছে, এর ভিত্তিতে পুরো ঢাকার চিত্র তুলে ধরা বা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক নয়।’[২]

করোনার অ্যান্টিবডি নিয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি প্রতিষ্ঠানের এই গবেষণাকে ‘প্রিলিমিনারি’ বলছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা মনে করেন, অ্যান্টিবডি টেস্টটা যথেষ্ট নয়। গবেষণাটা আরও বেশি মানুষকে নিয়ে করলে সেটি প্রতিনিধিত্বমূলক হতো বলেও মত প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা। গবেষণা প্রক্রিয়ার মধ্যেও ঘাটতির কথা বলছেন কেউ কেউ। গবেষণাটির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, ভাইরোলজিস্ট অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম ডয়চে ভেলেকে বলেছিলেন, ‘এটা কিন্তু রিয়েল টাইম ফাইন্ডিংস নয়। এরা এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত চার মাসের স্যাম্পল কালেকশন করেছে, এরপর গড় করেছে। সুতরাং আমরা অনেক কিছুই জানতে পারছি না। আমরা জানি না, কোন মাসে কত ছিল। আমি বলব, এটা প্রিলিমিনারি একটা রিপোর্ট হলো। এটার বিস্তারিত অ্যানালাইসিস করার সুযোগ আছে। আন্তর্জাতিকভাবে গবেষণাটি যথেষ্ট মূল্য দেবে। অ্যান্টিবডি ডেভেলপের ক্ষেত্রে বস্তিগুলো অনেক অগ্রসর হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ কীভাবে বুঝবে কোন মাসে কত সংক্রমণ ছিল? গবেষণার কাজটা হলো ঠিকই, কিন্তু আমরা এর মধ্য থেকে কিছু বের করতে পারলাম না। বিষয়টি এমন, আমাদের সামনে খাবার দেয়া হলো, কিন্তু আমরা খেতে পারলাম না।’
আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রেখে গবেষণাটি হয়েছে কিনা— এমন প্রশ্নের জবাবে অনুজীব বিজ্ঞানী ডা. সমীর কুমার সাহা ডয়চে ভেলেকে বলেছিলেন, ‘দেখুন প্রতিষ্ঠান দুটি কিন্তু গবেষণা করে। আমরা তো এখনও বিস্তারিত পাইনি। এটা যখন আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রচার হবে, তখন আমরা নিশ্চয়ই বিস্তারিত জানতে পারব। তখন তো এটা নিয়ে রিভিউ হবে। তখন সবাই বুঝতে পারবে। আমরা ধারণাই করেছি, এমন একটা পজিটিভিটি রেট হবে। আমাদের চিন্তাও ছিল এ রকম। কিন্তু আমি একটু অবাক হয়েছি এটার জন্য যে, জুলাই মাসে যদি এত বেশি পজিটিভ দেখা যায় তাহলে এটা তো বড় ব্যাপার। মনে হচ্ছে, এই সময়ের মধ্যে আমরা সবাই অ্যান্টিবডি পেয়ে গেছি। আমরা যদি আরও বড় করে স্টাডিটা করতে পারি তাহলে হয়তো ভালো হবে। তবে যেটা এসেছে সেটা আমাদের জন্য গুড নিউজ। আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। বিশেষ করে আমাদের বস্তিবাসীদের ক্ষমতা আরও বেশি। আমরা যারা গ্রামেগঞ্জে থাকিনি, তাদের হয়তো একটু কম প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। গবেষণাটি আরও বেশি সংখ্যায়, বেশিদিন ধরে করার প্ল্যান নিশ্চয়ই হবে।’
তবে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতেই গবেষণাটি হয়েছে বলে আইইডিসিআরের পরিচালক ডা. তাহমিনা শিরিন মনে করেন। তিনি ডয়চে ভেলেকে বলেছিলেন, ‘গবেষণাটি স্বল্প পরিসরে হয়েছে। কারণ, এখানে অনেক বিষয় সম্পৃক্ত। আমি চাইলেই ঢাকা শহরব্যাপী করতে পারব না। আমার ম্যানপাওয়ার লাগবে, রি-এজেন্ট লাগবে। সবকিছুর মূলে কিন্তু প্রাপ্যতা এবং অর্থ। এগুলোর জোগান কিন্তু কেউ দেয়নি। এগুলো আমাদের বিভিন্নভাবে ম্যানেজ করতে হয়েছে।’[৩]
[২. কাদির কল্লোল, ‘ঢাকার অর্ধেক মানুষ আক্রান্ত : সামনে তাহলে কী হবে!’, ১৩ অক্টোবর ২০২০, বিবিসি বাংলা; ৩. সমীর কুমার দে, ‘ঢাকায় অ্যান্টিবডি : স্বস্তির গবেষণায় সীমাবদ্ধতা’, ১৪ অক্টোবর ২০২০, ডয়চে ভেলে]

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের সাবেক পরিচালক ড. বে-নজীর আহমেদ বিবিসি বাংলাকে গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ব্যাপারে বলেছিলেন, ‘গবেষণায় যখন ৪৫ ভাগ বলছে, তখন আমাদের ধরে নিতে হবে যে, ঢাকায় এক কোটি মানুষ কোনো না কোনো সময় আক্রান্ত হয়েছে। এছাড়া খুব আলোচনা হচ্ছিল যে, আমাদের দেশের খেটে খাওয়া মানুষ বা বস্তির মানুষ সম্ভবত করোনায় আক্রান্ত হয় না। এই মিথটা যে ভুল, সেটা এই গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। বস্তির মানুষও আক্রান্ত হয়েছে এবং তারা ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়েছে। তাদের লক্ষণ কম হয়েছে এবং তারা উপসর্গ চেপে গেছে জীবিকার স্বার্থে। সুতরাং আমাদের দেশের ১৭ কোটি মানুষই এখন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।’
অন্যদিকে, বড় অংশের মানুষের দেহে যখন অ্যান্টিবডি পাওয়া গেছে, তখন হার্ড ইমিউনিটি বা প্রাকৃতিকভাবে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হবে কিনা— এই প্রশ্নেও আলোচনা চলছে। তবে এর সম্ভাবনা কম বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। আইইডিসিআরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এ এস এম আলমগীর বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন, ‘পরিস্থিতিটা ঝুঁকিপূর্ণ। সংক্রমণ যেহেতু উপসর্গহীনই বেশি ফলে আমার, আপনার আশেপাশে কে করোনাভাইরাস নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমরা কেউ সেটা জানি না। মাস্ক ছাড়া উপসর্গহীন রোগী ঘুরে বেড়ায়, সেও কিন্তু এই ভাইরাস ছড়াচ্ছে এবং আমি, আপনি যতই সতর্কতা অবলম্বন করি না কেন, আমাদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। হার্ড ইমিউনিটি নিয়ে অনেকে কথা বলছেন, এটা আসলে বৈজ্ঞানিকভাবে একেবারেই ঠিক নয়। কারণ করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে যে অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করে, সেটার পরিমাণ অনেক কম এবং দেড়-দুই মাসের মাথায় আবার কমতে শুরু করে। আর যাদের ক্রিটিক্যাল অবস্থা থাকে, তাদের শরীরে অ্যান্টিবডির পরিমাণ একটু বেশি থাকে। কিন্তু সেটাও তিন মাস থেকে কমতে শুরু করে এবং ছয় মাস পর অ্যান্টিবডি আর থাকে না। বিভিন্ন দেশে দ্বিতীয় দফায় অনেকে আক্রান্ত হয়েছে। বাংলাদেশেও দ্বিতীয় দফায় আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।’
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরাও এ ব্যাপারে বিবিসিকে বলেছিলেন, ‘অনেকের মনে হতে পারে যে, এতজনের যেহেতু অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করেছে, ফলে আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ নেই। বিষয়টা কিন্তু তাও নয়। দ্বিতীয় দফায় ইনফেকশন হচ্ছে, এমন উদাহরণ বিভিন্ন দেশে পাওয়া গেছে। সুতরাং আমি বলতে চাই যে, আমাদের যাতে দ্বিতীয় ওয়েভে আরেকবার সংক্রমণ না বাড়ে, সেজন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিরোধ করাটাই একমাত্র উপায়। এখানে স্বস্তি বা অন্য কোনো রকম আশংকা, কোনোটাই নেই।’[৪]
[৪. কাদির কল্লোল, ‘ঢাকার অর্ধেক মানুষ আক্রান্ত : সামনে তাহলে কী হবে!’ বিবিসি বাংলা, ১৩ অক্টোবর ২০২০]
দেশের কত মানুষ আসলে করোনায় আক্রান্ত
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত তথ্যের বাইরেও অসংখ্য মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেয়া প্রতিদিনের তথ্য অনুসারে, সারাদেশে এখন পর্যন্ত করোনা শনাক্ত হয়েছেন তিন লাখ ৯৬ হাজার ৪১৩ জন (২৩ অক্টোবর পর্যন্ত)। কিন্তু গবেষণা বলছে, শুধু ঢাকাতেই করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় এক কোটি মানুষ। এত পার্থক্য কীভাবে সম্ভব! বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খানা জরিপ আর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মোট হিসাব-কে কোনোভাবেই তুলনা করা যাবে না, কোনো দেশেই কেউ করবে না। বাংলাদেশের এই যৌথ গবেষণার মতো একই রকম স্টাডি ভারতের মুম্বাই, পুনে এবং দিল্লিতে হয়েছে। সেখানেও শনাক্ত হওয়া রোগীর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি মানুষ আক্রান্ত হওয়ার তথ্য এসেছে। মূল বিষয় হলো, দেশে সংক্রমণ ব্যাপক হলেও সেটা মানুষ বুঝতে পারেনি। জনস্বাস্থ্যবিদদের ধারণা ছিল, প্রচুর মানুষ আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু সেটা যে এত বেশি তা ধারণার বাইরে ছিল।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাবের বাইরে থাকার প্রধান কারণ হলো, ৮২% মানুষই লক্ষণ, উপসর্গবিহীন। লক্ষণ না থাকায় তারা পরীক্ষা করাতে যাননি। উদাহরণ দিয়ে জনস্বাস্থ্যবিদরা বলছেন, ১০০ জনের পরীক্ষাতে উপসর্গহীন ৮২ জনকে প্রথমেই বাদ দিলে বাকি থাকে ১৮ জন। এই ১৮ জনের মধ্যে কিছু মানুষ পরীক্ষা করাতে গেছেন আবার অনেকেই উপসর্গ থাকার পরও পরীক্ষা করাননি। বাসাতেই চিকিৎসা নিয়েছেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যে তথ্য আমরা পাই, সেটা হচ্ছে শুধু পরীক্ষা করাতে আসা মানুষের। এছাড়া মানুষ পরীক্ষা করেছে কম, অনেকে চিকিৎসা নেয়নি, বাড়ির কাছের ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কিনে খেয়েছে। যার কারণে করোনা আক্রান্ত হয়েও মানুষ বুঝতে পারেনি। তাই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য আর এই গবেষণার তথ্যে মিল না থাকাটাই স্বাভাবিক বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।
তবে প্রশ্ন থেকে যায় যে, সংক্রমণের হারের বিশাল এই পার্থক্য নিয়ে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যে সংক্রমণ হার দেখাচ্ছে সেটা বাস্তব সংক্রমণ হারের সঙ্গে কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিশাল তারতম্যের কারণ কী, সেটা নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। অনেকে মনে করেন, টেস্ট কম হওয়ার কারণে করোনার সংক্রমণ বোঝা যায়নি। আক্রান্ত রোগীর তুলনায় টেস্টের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। দেশে করোনা সংক্রমণের পরে গবেষকরা বারবার পরীক্ষা বাড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছিলেন। কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) টেস্টের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখে। একই সময় অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো বারবার করোনা টেস্ট করার আবদেন জানিয়েও সাড়া পায়নি সরকারের কাছ থেকে। অথচ যতদিনে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো করোনার পরীক্ষা শুরু করার অনুমতি পেল ততদিনে দেশে করোনা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে।
অনেকে বলছেন, করোনার সংক্রমণ হার কম দেখানো সরকারের স্ট্র্যাটেজির মধ্যে পড়ে। সংক্রমণের হার হুবহু গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী না হলেও এত তারতম্যপূর্ণ হতো না। সংক্রমণের হারের এত তারতম্য গ্রহণযোগ্য নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে, সব দেশেই শতকরা ১০% মানুষ আক্রান্ত হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। সেই হিসাবে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার হিসাবে আক্রান্ত হয়েছে এক কোটি ৬০ লাখ মানুষ। আর ঢাকাতেই যদি এক কোটি মানুষ আক্রান্ত হয় তাহলে বাকি সংক্রমণ ঢাকার বাইরে হয়েছে। ঢাকার বাইরে সংক্রমণের হার কম থাকার প্রসঙ্গে আইইডিসিআরের পরামর্শক ডা. মুস্তাক হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেছিলেন, ‘যারা শুধু পরীক্ষা করাতে আসছেন, তার বাইরে শুধু কন্টাক্ট ট্রেসিংয়ের সময়ে লক্ষণ-উপসর্গহীন মানুষকে পরীক্ষা করা হচ্ছে, এর বাইরে লক্ষণ না থাকলে পরীক্ষা হচ্ছে না। তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত তথ্যে এসব উপসর্গহীন মানুষের তথ্য যে একদম পাওয়া যায় না, তা নয়। তবে অধিকাংশই পাওয়া যায় না। এর আগে ২০০৯ সালে সোয়াইন ফ্লুর সময়ও সেরো প্রিভ্যালেন্স করে দেখা গেছে, কমপক্ষে ১০ গুণ মৃদু লক্ষণযুক্ত রোগী সার্ভিল্যান্সের বাইরে থাকে আর সর্বোচ্চ থাকে ৪০ গুণ। ১০ থেকে ৪০ গুণ রোগী ল্যাবরেটরি শনাক্তের বাইরে থাকে। বাংলাদেশেও করোনায় যা শনাক্ত হচ্ছে, তার কমপক্ষে ১০ গুণ, সর্বোচ্চ ৪০ গুণ রোগী বাইরে থাকছেন। কিন্তু ঢাকাতে আমার অনুমানে ৮০ গুণ রোগী বাইরে থাকছেন। তবে ঢাকার বাইরে সংক্রমণের হার রাজধানীর মতো হবে না, কম হবে।’
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মোট শনাক্তের বাইরেও অনেক রোগী থেকেছেন এবং এটাই স্বাভাবিক নিয়ম— মন্তব্য করে কোভিড-১৯ বিষয়ক জাতীয় পরামর্শক কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডা. শহীদুল্লাহ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেছিলেন, ‘সারা পৃথিবীতে যত রোগী শনাক্ত হয়, তার চেয়ে সর্বনিম্ন ১০ গুণ বেশি মানুষ থাকেন আনআইডেন্টিফায়েড। ভারত, আমেরিকাতেও একই রিপোর্ট, কারণ সবাই পরীক্ষা করতে যান না। বিশ্বে এজন্যই সেরোসার্ভিল্যান্স করা হয়। সেরোসার্ভিল্যান্স হচ্ছে র্যাপিড অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করে লক্ষণযুক্ত এবং লক্ষণছাড়া অথবা মৃদু লক্ষণ— সবমিলিয়ে কত মানুষ ইতোমধ্যে আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হয়েছেন সেটা পরীক্ষা করা।’[৫]

করোনায় দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু
করোনাভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করে যারা সুস্থ হয়ে উঠেছেন, তাদের ক্ষেত্রেও মাত্র এক মাসের মধ্যে এই রোগের বিরুদ্ধে শরীরে গড়ে ওঠা প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে যেতে পারে বলে একটি গবেষণায় উঠে এসেছে। ওই গবেষণার বরাত দিয়ে যুক্তরাজ্যের দৈনিক দ্য গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়েছে, সাধারণ ঠান্ডা, জ্বর, কাশির মতোই এই রোগও মানুষকে বছরের পর বছর আক্রান্ত করে যেতে পারবে। যুক্তরাজ্যের গাই'স অ্যান্ড সেন্ট থমাস ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের ৯০ জন রোগী ও স্বাস্থ্য সেবাকর্মীর ওপর কয়েক মাস ধরে চালানো এই গবেষণায় দেখা যায়, রোগীর দেহে লক্ষণ প্রকাশের প্রায় তিন সপ্তাহ পর পর্যন্ত ওই অ্যান্টিবডি ভাইরাসটি ধ্বংস করতে পারে। তবে ধীরে ধীরে তা হ্রাস পেতে থাকে।
রক্ত পরীক্ষায় দেখা গেছে, ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় ৬০ শতাংশ মানুষের দেহে ‘শক্তিশালী’ অ্যান্টিবডি কাজ করেছিল। তবে এর তিন মাস পর মাত্র ১৭ শতাংশের দেহে ওই অ্যান্টিবডি একইভাবে কাজ করে। আবার অ্যান্টিবডির স্তরগুলোও আগের তুলনায় ২৩ গুণ কমে যায়, অনেকক্ষেত্রে তাদের খুঁজেও পাওয়া যায় না।
এই গবেষণাদলের প্রধান লন্ডনের কিংস কলেজের অধ্যাপক ড. কেটি ডোরস বলেন, ‘ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মানুষের দেহে মোটামুটি ঠিকঠাক মাত্রাতেই অ্যান্টিবডি গড়ে উঠেছিল তবে অল্প সময়ের ব্যবধানে এটি কমা শুরু করে। রোগের কোন মাত্রায় শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে তার ওপর নির্ভর করে অ্যান্টিবডিগুলো শরীরে কতদিন অবস্থান করবে।’ করোনার বিরুদ্ধে মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নানাভাবেই লড়াই করতে পারে। তবে সেই লড়াইয়ের সম্মুখভাগে যদি অ্যান্টিবডি থাকে তবে এই গবেষণার ফলাফল বলছে, অ্যান্টিবডি যেহেতু স্থায়ী হচ্ছে না তাই সিজনাল অন্যান্য অসুখের মতো মানুষ করোনাতেও বারবার আক্রান্ত হতে পারে এবং এক্ষেত্রে ভ্যাকসিন তাদের দীর্ঘ সময় রক্ষা করতে পারবে না।[৬]
[৫. জাকিয়া আহমেদ, ‘দেশের কত মানুষ আসলে করোনায় আক্রান্ত?’ ১৪ অক্টোবর, ২০২০, বাংলা ট্রিবিউন; ৬. ‘করোনায় দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কতোটুকু?’, ১৪ জুলাই ২০২০, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড]
বাংলাদেশে করোনার দ্বিতীয় আঘাতের সম্ভাবনা কতটুকু
যেকোনো মহামারির দুই তিনটি ওয়েভ থাকতে পারে। জার্মানি, স্পেন, ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশে স্কুল-কলেজ খুলে দেবার পর বেড়ে যায় করোনার সংক্রমণের হার। মূলত এটিই হলো সংক্রমণের দ্বিতীয় আঘাত। আইইডিসিআরের মতে, বাংলাদেশে সংক্রমণের প্রথম ধাপ এখনও শেষ হয়নি। দেশে মার্চে সংক্রমণ শুরু হবার পর প্রতি মাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে এক লাখ করে। সবচেয়ে বেশি মানুষ সংক্রমিত হয়েছিল মধ্য জুলাইয়ে। তবে কোরবানির ঈদের পর তা কিছুটা কমে যায়। আইইডিসিআর জানিয়েছিল, আগস্টের শেষের দিকে সংক্রমণ যেভাবে কমতে শুরু করেছে তা যদি আরও দুই সপ্তাহ অব্যাহত থাকে তবেই ধরে নিতে হবে করোনাভাইরাস সংক্রমণের প্রথম আঘাত পার করেছে বাংলাদেশ। এরপর বোঝা যাবে দ্বিতীয় আঘাত কবে আসবে বা কবে শুরু হয়েছে বা শুরু হলেও সেটা কতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।
সামনে শীত। শীতে যে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে যায়, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যেসব দেশে শীতে তাপমাত্রা শূন্য বা তার কাছাকাছি থাকে সেসব দেশে করোনা আবারও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। তবে বাংলাদেশে ইউরোপের মতো শীতকালে তাপমাত্রা ততটা নেমে যায় না। তাই শীতকালে দেশে করোনার প্রকোপ অতটা বাড়বে না বলেই ধারণা আইইডিসিআরের। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে সতর্ক করেছেন যে, শীতকালে করোনার সংক্রমণ বাড়তে পারে। তিনি শীতে করোনা ঠেকাতে সকল প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকও ‘দ্বিতীয় ঢেউ’-এর আশঙ্কার কথা বলেছেন এবং এটাও বলেছেন যে, বাংলাদেশ করোনার দ্বিতীয় সংক্রমণ ঠেকাতে প্রস্তুত। গত ২৩ সেপ্টেম্বর তিনি এ কথাও বলেছেন যে, বাংলাদেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হয়েছে।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী করোনা ঠেকাতে বাংলাদেশ প্রস্তুত বলে যে ঘোষণা দিয়েছেন, সেটা করোনার প্রথম ঢেউ বাংলাদেশে আঘাত হানার সময়ের মতো কি-না, তা অবশ্য তিনিই ভালো বলতে পারবেন।[৭] তুরস্কের বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি গত ২৩ সেপ্টেম্বর জানায়, করোনাভাইরাসের ‘দ্বিতীয় ঢেউ’ বাংলাদেশে আঘাত হেনেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, করোনাভাইরাস পরিপূর্ণভাবে নির্মূল করা যাবে না এবং একটি ‘দ্বিতীয় ঢেউ’ ইতোমধ্যে আঘাত হানতে শুরু করেছে। ‘ইউরোনিউজ’ গত ৯ অক্টোবর জানিয়েছে, করোনাভাইরাসের ‘দ্বিতীয় ঢেউ’ এরই মধ্যে আঘাত হানতে শুরু করেছে। তারা কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের নামও উল্লেখ করেছে, যেখানে ভাইরাসটি আঘাত হেনেছে। ব্রিটেনের মতো দেশও এই তালিকায় রয়েছে। এদিকে আবারও ‘লকডাউনের’ মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বা হতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।
বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরাও আশঙ্কা করছেন যে, স্বাস্থ্যবিধি না মানলে ‘দ্বিতীয় ঢেউ’-এ মৃত্যুর সংখ্যা বাড়বে। বাংলাদেশে স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে না, সর্বত্র একটা ঢিলেঢালা ভাব, মানুষ গাদাগাদি করে বাসে ভ্রমণ করছেন, মার্কেটগুলোতে মানুষের ভিড়— সবমিলিয়ে বাংলাদেশকে নিয়ে একটা ভয়ের কারণ রয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে, বাংলাদেশ এখনও করোনার প্রথম ঢেউ সামলাচ্ছে। তবে আসন্ন শীতে সাধারণ ফ্লুর সঙ্গে কোভিড যোগ হয়ে পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার আশঙ্কা করছেন তারা। তারা বলছেন, মহামারি মোকাবিলায় স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপর আস্থার সংকট কাটাতে হবে সবার আগে। পরীক্ষার সুযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি প্রস্তুত রাখতে হবে হাসপাতালগুলোকে। বিভিন্ন পর্যায় থেকে শীতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আঘাত হানার আশঙ্কা করা হলেও তাপমাত্রার সঙ্গে কোভিড নাইনটিন ভাইরাসের কার্যকারিতা কম-বেশি হওয়ার বিশ্বাসযোগ্য গবেষণা এখনও পাওয়া যায়নি।
ন্যাশনাল টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজরি কমিটির বিভাগীয় সদস্য ডা. আবু জামিল ফয়সাল দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন, ‘শীতকালে মানুষ সাধারণত জ্বর, কাশি, হাঁচি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ভাইরাসজনিত বিভিন্ন (সর্দি) রোগে আক্রান্ত হয়। অন্যদিকে, করোনাভাইরাস শীত আবহাওয়ায় দীর্ঘকাল ধরে বেঁচে থাকতে পারে। তাই এ সময় সংক্রমণের হারের ক্ষেত্রে একটা উত্থান দেখা দিতে পারে। শীতকালে ভাইরাসটির সম্ভাব্য ঢেউয়ের বিষয়ে আমরা সরকারকে সতর্ক করেছি এবং তা মোকাবিলায় যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছি।’ তবে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক নজরুল ইসলাম। তার মতে, অন্যান্য ভাইরাস ও ফ্লু জাতীয় রোগের কারণে পরিস্থিতির এতটা অবনতি নাও হতে পারে। তিনি দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন, ‘অন্যান্য ভাইরাসের প্রকোপের কারণে শীতকালে করোনা আরও দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। এটি আমার অনুমান, তবে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত এবং সবধরনের প্রতিরোধমূলক প্রস্তুতি নিয়ে রাখা উচিত। কেননা বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ঋতুতে করোনার আলাদা আলাদা রূপ দেখা যাচ্ছে।’[৮]
[৭. কামাল আহমেদ, ‘সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ের বাস্তবতা ও সতর্কতা’, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০, প্রথম আলো; ৮. আবদুর রহমান জাহাঙ্গীর, ‘শীতে কোভিডের সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ মোকবিলায় বিশেষজ্ঞরা যা পরামর্শ দিচ্ছেন’, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০, ইউএনবি নিউজ]
দ্বিতীয় আঘাতে কত মানুষ আক্রান্ত হতে পারে
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আঘাত হেনেছে। যার মধ্যে ব্রিটেন অন্যতম। দেশটিতে একদিনেই (১৭ অক্টোবর) ১৬ হাজার ১৭১ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এবং করোনায় আক্রান্ত হয়ে একদিনেই মারা গেছেন ১৩৬ জন। অথচ গত ২৮ দিনে দেশটিতে করোনায় মৃতের সংখ্যা ছিল ১৫০ জন।[৯] এদিকে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসসহ আরও আট শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছে। শনিবার (১৭ অক্টোবর) থেকে আগামী ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত এ কারফিউ পালনের নির্দেশ দেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ।[১০] করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ভয়াবহভাবে বেড়ে যাওয়ায় দ্বিতীয়বারের মতো দেশব্যাপী লকডাউন জারি করেছে চেক প্রজাতন্ত্র সরকার। অক্টোবরের ৫ তারিখ থেকে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। মাস্ক সব জায়গায় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গির্জায় ১০ জনের বেশি মানুষের প্রবেশ নিষেধ করা হয়েছে। শপিং সেন্টারগুলোতে ওয়াইফাই বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে, যাতে তরুণদের জমায়েত কম হয়।[১১]
স্পেনে সংক্রমণ কমাতে মন্ত্রিসভা ১৫ দিনের জরুরি অবস্থা জারির নির্দেশ দিয়েছে। সারাদেশে কোয়ারেন্টাইন পদ্ধতি আবারও বলবৎ হচ্ছে। করোনাভাইরাসের মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে রাশিয়ায় একদিনে রেকর্ড সংখ্যক লোক আক্রান্ত হয়েছে। দেশটিতে ১৩ অক্টোবর ১৩ হাজারের বেশি নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে।[১২] সারাবিশ্বের যখন এই অবস্থা তখন বাংলাদেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আঘাত হানলে কত সংখ্যক লোক আক্রান্ত হতে পারে এ নিয়ে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। কারণ বাংলাদেশ করোনার প্রথম ঢেউয়েই সংক্রমণের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে পারেনি। সম্প্রতি আইসিডিডিআরবি ও আইইডিসিআরের যে যৌথ সেরোসার্ভের কথা বলা হয়েছে সেটি নিয়েও বিতর্ক আছে। এটি একধরনের জরিপ যেখানে বিজ্ঞানী বা সরকারি কর্মকর্তারা আক্রান্তদের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে অ্যান্টিবডির খোঁজ করেন। বিভিন্ন কারণে সেরোসার্ভের ফলাফল ভুল হতে পারে। পরীক্ষকদের হাতে অন্য ভাইরাসের অ্যান্টিবডি আসতে পারে। অনেক টেস্টেই সামান্য পরিমাণে অ্যান্টবডি থাকলে তা ধরা পড়ে না। অনেক মানুষ, বিশেষ করে তরুণদের শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হওয়া ছাড়াই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই চলে। ফলে করোনায় আক্রান্ত হলেও পরীক্ষার ফলাফল ভুলে নেগেটিভ আসতে পারে। তবে আমাদের উচিত কত সংখ্যক মানুষ করোনার দ্বিতীয় ধাপে আক্রান্ত হবে সে বিষয়ে আলোচনা না করে সংক্রমণ কীভাবে কমানো যায়, সেটা নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা করা।
আড়ালে থেকে যাচ্ছে অনেক তথ্য
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেয়া তথ্য থেকে আমরা করোনার দৈনিক ও মোট সংক্রমণের সংখ্যা, দৈনিক ও মোট মৃত্যুর সংখ্যা, দৈনিক ও মোট টেস্টের সংখ্যা, দৈনিক ও মোট সুস্থের সংখ্যা জানতে পারছি। কিন্তু এসব তথ্যের বাইরে থেকে যাচ্ছে ‘জ্বর-কাশি-শ্বাসকষ্টে’ মারা যাওয়াদের একটা বড় সংখ্যা। ভয়েস অব আমেরিকার তথ্য অনুযায়ী, মার্চে দেশে প্রথম করোনা সংক্রমণের পর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত দেশে জ্বর-সর্দি-কাশি-গলাব্যাথায় মারা গেছেন ৫৮ জন। কিন্তু তাদের মৃত্যু করোনাতে হয়েছে কিনা, তা নিরূপণ করা যায়নি। ‘জ্বর-কাশি-শ্বাসকষ্টে’ মারা যাওয়াদের একটা বড় সংখ্যা, যাদের করোনায় মৃত্যুর বিষয়টি অস্বীকার করে প্রশাসন মৃতদের পরিবার ও তার আশপাশের বাড়িঘর লকডাউন করে রাখে। বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরের ভিত্তিতে সেসব অতালিকাভুক্তদের তালিকাভুক্ত করে ‘বিডিকরোনাইনফো’ নামক একটি আনঅফিসিয়াল ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট জানায়, ৮ এপ্রিল পর্যন্ত (৯ এপ্রিলের তথ্য যুক্ত হয়নি তখনও) করোনাভাইরাসে বেসরকারি হিসাবে ১০৭ জন এবং সরকারি হিসাবে ২০ জনসহ মোট মারা গেছেন ১২৭ জন।
করোনাভাইরাস আর ইনফ্লুয়েঞ্জার মধ্যকার অনেক মিল সত্ত্বেও পার্থক্যের বড় জায়গা হলো, ভাইরাসটি জ্বর, খুসখুসে শুকনা কাশি উপসর্গের পাশাপাশি ফুসফুস আক্রান্ত করে ভয়াবহভাবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রথম আলোর গত ৩১ মার্চের একটি প্রতিবেদন জানাচ্ছে যে, গত বছরের মার্চের তুলনায় এই বছরের মার্চে শ্বাসতন্ত্রে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১৪ গুণ। এ বছরের মার্চ মাসের শেষদিনটি পর্যন্ত আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ৯৩০ জন, যেটা আগের বছরের একই মাসে ছিল মাত্র ৮২০ জন।[১৩] এত বিপুল সংখ্যক রোগী বাড়ার পেছনে করোনা দায়ী কিনা বা এসব রোগী আসলে করোনায় আক্রান্ত ছিলেন কিনা— এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার দায়িত্ব ছিল সরকারের। কিন্তু তখনও করোনার পরীক্ষাই দেশে ভালোমতো শুরু হয়নি। বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে যারা মারা যাচ্ছেন তাদের একটি বড় অংশ এখনও থেকে যাচ্ছেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাইরে। আমাদের দেশে প্রথমদিকে যখন উপসর্গ নিয়ে রোগীরা মারা যাচ্ছিলেন তখন তাদের হিসাবেই আনা হয়নি।
[৯. ‘করোনার দ্বিতীয় ঢেউ : ব্রিটেনে একদিনে ১৬ হাজারের বেশি রোগী শনাক্ত’, ১৮ অক্টোবর ২০২০, ইত্তেফাক; ১০. ‘করোনাভাইরাসের কারণে ফ্রান্সের ৯ শহরে কারফিউ জারি’, ১৮ অক্টোবর ২০২০, দ্য ডেইলি ইনকিলাব; ১১. ‘চেক প্রজাতন্ত্রে জাতীয় পর্যায়ে লকডাউন জারি’, ১৪ অক্টোবর ২০২০, ডয়চে ভেলে; ১২. ‘করোনার দ্বিতীয় ঢেউ : একদিনে রাশিয়ায় রেকর্ড আক্রান্ত’, ১৩ অক্টোবর ২০২০, ইত্তেফাক; ১৩. প্রণোদনা শামীমা বিনতে রহমান, ‘কোভিড-১৯ : স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রতারণা ও প্রধানমন্ত্রীর হয়রানি’, ১০ এপ্রিল ২০২০, নেত্র নিউজ]

গত ১৫ মে বিবিসি বাংলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি জরিপ উল্লেখ করে বলেছিল, করোনাভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে ৯২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে যাদের কারও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়নি। বাংলাদেশে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় ৮ মার্চ। ওইদিন থেকে গত ৯ মে পর্যন্ত বাংলাদেশের ২৪টি গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে এই জরিপ প্রস্তুত করা হয়। জরিপটি পরিচালনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ (সিজিএস)। সিজিএসের পরিচালক ইমতিয়াজ আহমেদ তখন বিবিসিকে জানিয়েছিলেন যে, ‘করোনাভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে এই মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি বলে তিনি আশঙ্কা করছেন। যারা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন তাদের যেমন লিস্টেড করা যায়নি, একইভাবে যারা এই উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাদের ট্রেসিং করতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার।’[১৪] সুতরাং এখানে দুটা বিষয় আলোচনায় আসে। যারা মারা গেছেন তারা করোনায় আক্রান্ত ছিলেন কিনা, আর তারা কতজনকে সংক্রমিত করে গেছেন। এসব হিসাব যেহেতু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সংগ্রহ করেনি বা করতে পারেনি, সেই হিসাবে স্বাভাবিক নিয়মেই তাদের কাছে সংক্রমণের হারের বাস্তব চিত্র আশা করা যায় না।
দোষ কি শুধু সরকারের
অনেক মানুষের মধ্যে করোনা সম্পর্কে একধরনের ‘ড্যাম কেয়ার ভাব’ দেখছেন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ। সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ার কারণ হিসেবে আরেও কিছু বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। ডয়চে ভেলেকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আসলে জনগণের মধ্যে করোনা সম্পর্কে সহনশীলতা এসে গেছে। মানুষ করোনাকে পাত্তাই দেয় না। ভয় পায় না, তাদের মধ্যে ড্যামকেয়ার ভাব, উদাসীন ভাব। আসলে জনগণই নিয়ম মানছে না। এর প্রধান কারণ, মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য জীবিকা দরকার। এসব কারণে মানুষ নিয়ম মানছে না। অনেকেই মনে করছেন, করোনা হয়তো কোনোদিন যাবে না। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবন-জীবিকার স্বার্থে এভাবেই চলতে হবে। আসলে লকডাউন যেটা দেয়া হয়েছে সেটা মানুষই মানে না। পৃথিবীর কোথাও মানে না। শুধু আমাদের দেশ নয়। শুরুতে কিছুদিন মানুষ মেনেছিল। এরপর আর মানে না। গত দুই ঈদে জনগণকে আমরা বারবার বলেছি, যে যেখানে আছেন সেখানেই ঈদ করেন। কিন্তু কেউ কথা শোনেনি। এমনকি জার্মানির মতো দেশ, যারা উচ্চশিক্ষিত, সেখানেও (বার্লিন) মিছিল বের হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ মিছিল করেছে। তারা লকডাউন মানেনি। অন্য একটি ইউরোপিয়ান দেশ, যারা কারফিউ দিয়েছে কিন্তু সেটার বিরুদ্ধে মানুষ মিছিল করেছে। ইউরোপের অনেক দেশে এটা মানছে না। মানুষকে আসলে কতদিন বন্দি রাখা যায়। মানুষ এটা মানতে চায় না। আসলে রোগটা তো নতুন, সারা পৃথিবীতে কেউই জানত না। এই রোগ সম্পর্কে আমাদের ভালো আইডিয়াও ছিল না। কিন্তু রোগটা তো মারাত্মক ছোঁয়াচে। মানুষ যদি স্বাস্থ্যবিধি না মানে, ইচ্ছামতো চলাফেরা করে, তাহলে তো বাড়ার ঝুঁকি থাকবেই। আমাদের পরপর দুটি ঈদ গেল, গরুর হাট গেল, সেখানে তো স্বাস্থ্যবিধি মানার কোনো বালাই ছিল না। এসব কারণে তো সংক্রমণ বাড়ছে।[১৫]
[১৪. করোনাভাইরাস : বাংলাদেশে উপসর্গ নিয়ে নয়শ'র বেশি মৃত্যুর হিসেব বেসরকারি সংগঠনের, তদন্ত হচ্ছে কতোটা’, ১৫ মে ২০২০, বিবিসি বাংলা; ১৫. সমীর কুমার দে, ‘মানুষ করোনাকে পাত্তাই দিচ্ছে না’, ২১ আগস্ট ২০২০, ডয়চে ভেলে]
আমরা কিন্তু একদিনের জন্যও পুরো দেশে লকডাউন দেইনি। আমরা লকডাউন দেইনি, দিয়েছি সাধারণ ছুটি। এই ছুটির ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সরকার কিছু বিধিনিষেধ জারি করে। সে বিধিনিষেধগুলো মেনে চললে একধরনের লকডাউনই হয়ে যায়। অনেকের মতে, বিষয়টা আমাদের জন্য বুমেরাং হয়ে গেছে। এমনিতে লকডাউনে সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের। লাভ হয়, রোগটা ছড়াতে পারে না। আমাদের ছুটির সঙ্গে ঘোষিত বিধিনিষেধের কারণে অফিস-আদালত-কল-কারখানা বন্ধ থেকেছে। ফলে শুরুতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বলতে গেলে বন্ধই ছিল। আবার ‘ছুটি’ শব্দটা থাকার কারণে সাধারণ মানুষের চলাচলের ওপর কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। এতে লকডাউনের যে লাভ, রোগ ছড়াতে না পারা, সেটা আর আমরা পাইনি। সাধারণ জনগণ ছুটি পেয়ে যার যার বাড়ির দিকে ছুটেছে। ফলে ভিড় বেড়েছে, জনসমাগম বন্ধের পরিবর্তে তা বেড়েছে। মানুষ সাধারণ ছুটির কারণটা অনুধাবন করতে পারেনি। এই ছুটির লক্ষ্য ছিল করোনার সংক্রমণ কমানো, ভাইরাসটি যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেটা নিশ্চিত করা কিন্তু জনগণ হিসেবে আমরা লকডাউনের ক্ষতিকর দিকটা অর্জন করেছি, কিন্তু লাভজনক দিকটা হারিয়েছি। বিশেষজ্ঞরা বারবার বলেছিলেন, করোনা সংক্রমণ ভয়াবহ হবে যাতায়াতের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ব্যর্থতার কারণে। ইমিডিয়েটলি তখন প্রভাবটা হয়তো বোঝা যায়নি। কিন্তু সংক্রমণগুলো কিন্তু ওই সময়টাতেই বেশি হয়েছে।
লেখক : টেকনিক্যাল অপারেশনস ডিরেক্টর, এমিনেন্স অ্যাসোসিয়েটস ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট;
গবেষণা সহকারী : মো. আজিজুল হক
এমএআর/এমএস