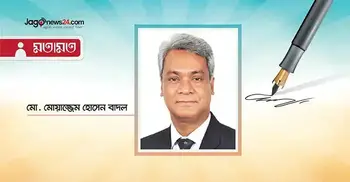হাসপাতালে ‘কয়েকটি ভাঙা হাড়’ যেন বাংলাদেশের প্রতিবিম্ব

বইটির মলাটে লেখা আছে- ‘হাসপাতাল বাংলাদেশে বহুল আলােচিত একটি প্রসঙ্গ। হাসপাতালকে ঘিরে এদেশের মানুষের আছে নানা প্রত্যাশা, ক্ষোভ। সশরীর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে লেখা এই বইয়ে চিকিৎসক, নার্স, রােগী, রােগীর আত্মীয়, ওয়ার্ডবয়, ঝাড়দার, আয়া প্রমুখদের নিয়ে গড়ে ওঠা হাসপাতাল জীবনের এক অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন শাহাদুজ্জামান।’
‘তিনি দেখিয়েছেন কী করে হাসপাতালের জীবন বস্তুত বাংলাদেশের বৃহত্তর সমাজের নানা বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফলিত করেছে। কী করে হাসপাতালের একটি ওয়ার্ড হয়ে উঠেছে একটি ক্ষুদ্র বাংলাদেশ।’ বইটি একজন নৃবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে একটি হাসপাতালের একটি ওয়ার্ডের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ হলেও শেষমেষ যেন সেটা হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের প্রতিবিম্ব।
পরিসংখ্যাননির্ভর গবেষণায় আমরা জানি Little about a lot পক্ষান্তরে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমরা জানি Lot about a little. অনেকটা খনি তুলবার মতো। খনির মুখটি ছোট, ভেতরটা গভীর। লেখক ২০০১ সালে প্রায় মাস পাঁচেক হাসপাতালের একটা ওয়ার্ডে নিয়মিত যাতায়াত করেছেন। বইটা একটা গবেষণা গ্রন্থ হলেও লেখকের চমৎকার বর্ণনাশৈলিতে হয়ে উঠেছে উপভোগ্য।
সর্বমোট আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটিতে হাসপাতালের ওয়ার্ডটির কর্মকাণ্ডকে এর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হাসপাতালে রোগীর পদমর্যাদা সবচেয়ে নিচে। ওয়ার্ডের ঝাড়ুদার থেকে প্রফেসর সবাই রোগীদের সুযোগ পেলেই বকাঝকা এবং অপদস্থ করে থাকেন। এই হাসপাতালের অধিকাংশ রোগীই মূলত নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত, দরিদ্র, অল্পবয়সী যুবক।
দেওয়ার মধ্যে হাসপাতাল রোগীদের দেয় একটি গদি বা বিছানা আর চিকিৎসকদের বিনামূল্যে পরামর্শ। কিন্তু চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র বা উপকরণের প্রায় সবটুকুই রোগীকে হাসপাতালের বাইরে থেকে কিনতে হয়। রোগীরা অধিকাংশ নিম্নবিত্ত অথচ পক্ষান্তরে চিকিৎসকরা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের প্রতিনিধি। হাসপাতালের নিম্নবিত্ত রোগীরা, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত ডাক্তারদের সেই কর্তৃত্বের মুখোমুখি হন, যে কর্তৃত্বের মুখোমুখি তারা হাসপাতালের বাইরে প্রাত্যহিক জীবনেও হয়ে থাকেন।
বাংলাদেশের মানুষের মনে এই সেন্স অব হায়ারার্কি অত্যন্ত গভীরে প্রথিত এবং তা ব্রতের মতো পালিত হয়। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কারণে রোগীদের যে অর্থনৈতিক ক্ষতি সেটি দেশের সামগ্রিক দারিদ্র্যের সঙ্গেই সম্পর্কিত।
পরিবার বাংলাদেশের সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি একক। একজন ব্যক্তির জীবনের প্রধান সিদ্ধান্তগুলো মূলত পরিবারকেন্দ্রিক। হাসপাতাল একভাবে যেন সেই পরিবারকেই প্রতিস্থাপন করে। পশ্চিমা হাসপাতালগুলোতে রোগীর আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা খুবই সীমিত। বাংলাদেশে রোগীর আত্মীয়-স্বজন হাসপাতাল ওয়ার্ডের কার্যক্রমের অনানুষ্ঠানিক কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।
ওয়ার্ডটাকে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অনেক কাজই রোগীর আত্মীয়-স্বজনরা করে থাকেন। হাসপাতালে ভর্তির পর থেকে ডিসচার্জের সময় পর্যন্ত রোগীর কোনো একজন নিকট-আত্মীয় রোগীর সঙ্গে থাকেন। রোগীর শুশ্রুষার প্রায় সবরকম কাজই মূলত রোগীর আত্মীয়-স্বজনরা করে থাকেন। হাসপাতালের কর্মচারী-কর্মকর্তাদের হাতে অপদস্থ হয়েও, নিজেদের ব্যবসা, কাজ, পারিবারিক জীবনকে বিঘ্ন ঘটিয়েও এবং নানারকম ব্যক্তিগত অস্বস্তি সত্ত্বেও রোগীর আত্মীয়-স্বজনরা হাসপাতালে রোগীর সঙ্গে থেকে যান।
তাদের বাড়িয়ে দেওয়া সাহায্যের হাত বাঁচিয়ে তুলছে রোগীকে, রক্ষা করে হাসপাতালের কর্মচারীদেরও, সচল রাখে হাসপাতালকে। রোগীর আত্মীয়-স্বজনরা তাই উভয়ের জন্যই অকূলের কূল। চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা ওয়ার্ডে এমন একটি অবস্থানে থাকেন যারা একদিকে রোগী আবার অন্যদিকে ডাক্তার এবং নার্স উভয়ের জন্যই অপরিহার্য। রোগীকে হাসপাতালের সামাজিকীকরণের জন্য নির্ভর করতে হয় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ওপর।
শ্রেণিগত ব্যবধানের কারণে রোগীরা ডাক্তার বা নার্সের কাছ থেকে রোগ অথবা হাসপাতাল বিষয়ে কোন তথ্য জোগাড় করতে সক্ষম হন না। ফলে শেষ পর্যন্ত হাসপাতালের কর্মচারীদের মধ্যে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের সঙ্গেই রোগীদের যোগাযোগ ঘটে সবচেয়ে বেশি। এমনকি মধ্যবিত্ত রোগীকেও বিবিধ কারণে নির্ভর করতে হয় চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ওপরই। যদিও অনেক কাজই তাদের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে কিন্তু ওয়ার্ডের অধস্তন কর্মচারীদের কাছ থেকে কোন কাজ পেতে হলে রোগীকে অবশ্যই বখশিশ দিতে হয়।
বখশিশের ব্যাপারটি কোনো গোপন বিষয় নয়। অবশ্য একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যেটি বখশিশ, প্রথম শ্রেণির কর্মচারীদের কাছে সেটা ঘুস। সরকারি প্রতিষ্ঠানে ঘুস কিংবা বখশিশের ব্যবহার তাই কাউকে এখন আর বিস্মিত করে না।
নার্সের বাংলা শব্দ ‘সেবিকা’। কিন্তু হাসপাতালের দৈনন্দিন জীবনে সেবিকা শব্দটির তেমন কোনো ব্যবহার নাই। বাংলাদেশের সরকারি হাসপাতালের নার্সরা নার্সিং-এর কাজ করেন সামান্যই। তাদের সময় পেরিয়ে যায় রিপোর্ট, রেজিস্টার, ফাইল এইসব ঠিকঠাক করতেই। চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজ তাদের খুবই কম। আর রোগীর পরিচর্যার কাজতো তারা মোটেই কিছু করেন না।
সে কাজটি মূলত করেন রোগীর আত্মীয়-স্বজনরা। নার্সকে পশ্চিমা গবেষকরা বলছেন ‘ছদ্মবেশী মা’। কিন্তু রোগীকে কোনোভাবে মানসিক শক্তি যোগানো, কাউন্সিলিং করা- এসব নার্সদের কখনও করতে দেখা যায় না। তারা রোগীর চাইতে বরং পরিণত হয়েছেন বিভিন্ন প্রশাসনিক কাগজপত্রের সেবিকায়। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল নার্স বলতে প্রদীপ হাতে আত্মত্যাগী মর্যাদাশীল নারীর যে চিত্র এঁকেছিলেন, বাংলাদেশি নার্সদের বেলায় সে চিত্র মেলে না। বাংলাদেশের নার্সরা বরং প্রদীপবিহীন, হতাশ একদল নারী যারা ওয়ার্ডে কেবলই ফাইল আর রেজিস্টার নিয়ে ছুটাছুটি করেন।
‘হাসপাতাল’ ডাক্তারদেরই রাজত্বের নাম। এ রাজ্যে তারাই রাজা। হাসপাতাল ডাক্তারদের আনন্দ, দম্ভ কিংবা ক্ষোভ প্রকাশের মাঠ। ডাক্তারদের মর্যাদাবোধ খুব টানটান কিন্তু নিজেদের পেশা নিয়ে তারা ভীষণভাবে হতাশ। ওর্য়াডটিকে যদি একটি মঞ্চ ভাবা যায় যেখানে চিকিৎসা নামের নাটক অভিনীত হচ্ছে, তাহলে বলতে হবে, প্রফেসর রাউন্ডটি হচ্ছে নাটকের ক্লাইম্যাক্স।
এ দৃশ্যতে প্রধান অভিনেতা হচ্ছেন প্রফেসর আর অন্যান্য জুনিয়র ডাক্তার আর নার্সরা হচ্ছেন পার্শ্ব চরিত্রের অভিনেতা অভিনেতা। ডাক্তারের সাথে রোগীর আলোচনার তেমন কোন চর্চা সরকারি হাসপাতালে নেই। ডাক্তাদের ভাষ্যমতে, পুরো দেশটাই যেখানে করাপ্ট সেখানে সব পেশার লোকই করাপ্ট। সবাই খালি টাকা বানাতে চায়, বড়লোক হতে চায়। ডাক্তাররাও তার ব্যতিক্রম নয়।
ডাক্তাররা যতই উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন হোন না কেন, যতই কতৃত্বপরায়ন হন না কেন ব্যক্তিগতভাবে তারা সকলেই একজন হতাশ, ক্ষুব্ধ মানুষ। ফলে দম্ভ আর হতাশার যুগলবন্দীতে আটকা পড়ে আছেন বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ডাক্তাররা।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ‘পৃথিবীতে এমন দেশ পাওয়া দুর্লভ যেখানে বাংলাদেশের মতো এত ক্ষুদ্র এলাকায় এত তীব্র দারিদ্র্য পুঞ্জিভুত হয়েছে।’ ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানি শাসনামলের পর স্বাধীন বাংলাদেশ একটা পঙ্গু অর্থিনীত নিয়ে প্রবেশ করেছে আন্তর্জাতিক মুক্ত বাজারে। স্বাধীনতার পর শাসকশ্রেণীর লুটেরা চরিত্র, আন্তর্জাতিক স্নায়ুযুদ্ধের প্রভাব, হত্যা ষড়যন্ত্রমূলক অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামরিক শাসন বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আর স্থিতিশীল হবার সুযোগ দেয়নি।
ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সামরিক বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, বাজেটের পাল্লাটিও তাই সেদিকে ভারি। তবুও উন্নয়ন গবেষকদের নান তত্ত্বকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অতি দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা, সম্পদের অতি দৈন্য, অতি অস্থির রাজনীতি মিলিয়ে এক অসম্ভব পরিস্থিতি পার করে বাংলাদেশ টিকে গেছে। আন্তর্জাতিক টেলিভিশনের খবরে কিংবা ত্রাণ সংস্থাগুলোর বিজ্ঞাপনে যেমন বাংলাদেশ দেখানো হয় বাংলাদেশিরা কিন্তু তেমন নিষ্ক্রিয় ভুক্তভোগী নয়। তারা সবাই কর্মী।
একজন নৃবিজ্ঞানী হিসেবে হাসপাতালের অর্থপেডিক ওয়ার্ডে প্রায় পাঁচ মাস অতিবাহিত করার পর লেখকের মনে হাসপাতালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব ছবি ভেসে উঠে। লেখক নিজেও ডাক্তার হিসেবে মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে অনেকদিন কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এই গবেষণাটি করতে যেয়ে তার মনেহয়েছে এ হাসপাতালকে যেন ঠিক আগে তিনি চিনতেন না। নতুনভাবে যেন চেনা হোটেল চিরচেনা জায়গাটিকে। লেখক লেখাটি তাই শেষ করেছেন T.S Eliot এর Little Gidding কবিতার কয়েকটি লাইন দিয়ে:
‘‘We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.’’
এমআরএম/জিকেএস