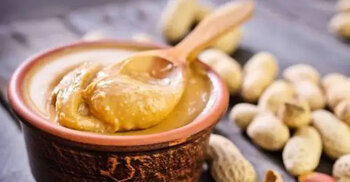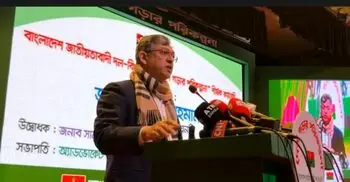আমরা কি বিদ্যুৎ রফতানি করবো?

আমরা বহু আগে থেকেই জানি, বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবিলায় আমাদের রয়েছে বিপুল সক্ষমতা। কিন্তু সেই সক্ষমতা কেন কাজে লাগেনি বা লাগানো হয়নি, সে প্রশ্ন ভিন্ন। ওই ভিন্ন প্রশ্নের জবাবদিহিতা করা গেলে প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসবে বা আসতো। সক্ষমতা থাকার পরও কেন উৎপাদন ১০/১১ হাজারে আটকে ছিল, তার কারণও অনুসন্ধান জরুরি। আবার ২৫,৭০০ মেগাওয়াটের সক্ষমতাকে কাজে না লাগিয়ে কেন ১০/১১ হাজার উৎপাদন করে দেশের মানুষকে লোডশেডিংয়ের ভেতরে ভরে দিয়েছিলেন তারা, তারও উত্তর খোঁজা জরুরি।
এখন দেশের প্রকৃত বিদ্যুৎ চাহিদা সর্বোচ্চ ১৪ হাজার মেগাওয়াট। সক্ষমতার ১১ হাজার ৭০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন উৎপাদন হয় না? এটি একটি প্রকাশ্য রহস্য। এই রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন না হলে এই খাতে বিনিযোজিত সরকারি অর্থ লোপাট হয়ে যাবে বা লোপাট হয়ে যাচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য। সক্ষমতার শক্তি যখন ২৫,৭০০, তারপরও সরকার ২০১৭ সালে ভারতের আদানি গ্রুপের আদানি পাওয়ারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তি অনুযায়ী আদানিপাওয়ার ১ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে শুরু করেছে দিনতিনেক আগে থেকে।
পাঁচ বছর ধরে আদানি পাওয়ারকে ক্যাপাসিটি চার্জ দিয়ে আসছে সরকার, মানে আমাদের সরকার। গত ৯ মার্চ দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল দিনের বেলায় ১০ হাজার ৮৪২ মেগাওয়াট আর রাতের বেলায় ১২ হাজার ৯৬ মেগাওয়াট। চাহিদার এই পরিমাণের চেয়ে দেড়গুণ উৎপাদন সক্ষমতা থাকার পরও ভিনদেশি বিদ্যুৎ আমদানি কেন? সেটা কি কেবল সক্ষমতা বাড়ানোর আয়োজন? সক্ষমতার বিপরীতে তো তা ব্যবহারের ক্ষেত্র তৈরি করা যায়নি বা হয়নি? আয়োজন যে নেওয়া হয়নি, তা নয়, কিন্তু সব আয়োজনই গতিহীন প্রগতির নিচে পড়ে আছে।
ব্যাপক শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের (ইজেড) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়েছিল সরকার। পাশাপাশি নেওয়া হয় নতুন কিছু শিল্প জোন ও শিল্প নগর নির্মাণের উদ্যোগও। এখন পর্যন্ত এগুলোর বাস্তবায়নের গতি নিয়ে তেমন সন্তুষ্ট নন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের মধ্যেও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে কম। (বণিক বার্তা/১১ মার্চ, ২০২৩)
এই রিপোর্টই বলে দিচ্ছে সরকারের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রাক্কলিত উন্নয়ন প্রকল্প এগিয়ে নিতে পারেনি। তার মানে ২০৩০ সাল নাগাদ আমাদের বিদ্যুৎ সক্ষমতা যতোটা বাড়বে, তা ব্যবহারের জন্য শিল্প সেক্টরে চাহিদা বাড়বে না বা বাড়াতে পারবে না সরকার। কারণ ওই সেক্টরের অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। এই ব্যর্থতা কি সরকারের নাকি বিপিডিবির? নাকি শিল্প মন্ত্রণালয়ের নাকি উদ্যোক্তাদের, যারা প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত পিডি তাদের নাকি যারা ওই সব অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য ডিজাইন করেছিলেন, তাদের ভুলেভরা প্রাক্কলন?
এই সব বিষয়ে যোগ্য, দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই। সরকার যদি আওয়ামী বিবেচনায় বেছে বেছে অদক্ষ ও অযোগ্যদের দায়িত্ব দেন, তাহলে এমনটাই হওয়ার কথা। এই ক্ষেত্রে অবশ্যই রাজনৈতিক পরিচয় নয়, যোগ্যতাই প্রধান হয়ে উঠতে হবে। কিন্তু আমরা তো দেখছি সরকার রাজনৈতিক পরিচয়ের অধীনে চলে গেছেন। যোগ্যতার বালাই নেই অনেক জায়গায়ই। অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্প জোন, শিল্প নগর নির্মাণের আয়োজনের পরও দেশীয় উদ্যোক্তাদের মধ্যে তেমন আগ্রহ নেই কেন, এ নিয়ে অবশ্যই পর্যালোচনা প্রয়োজন।
২.
দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা এখন ২৫ হাজার ৭০০ মেগাওয়াট (সরকারি আরেক হিসাব অনুযায়ী ২৬ হাজার ৭০০ মেগাওয়াট)। ২০২৭ সাল নাগাদ উৎপাদনে (আমদানিকৃতসহ) আসার কথা রয়েছে আরও ১৩ হাজার মেগাওয়াটের বেশি সক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্র। এছাড়া চুক্তি সইয়ের অপেক্ষায় রয়েছে আড়াই হাজার মেগাওয়াটের বেশি সক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্র।
সব মিলিয়ে ওই সময়ে দেশে বিদ্যুৎ খাতের উৎপাদন সক্ষমতা দাঁড়ানোর কথা ৪১ হাজার মেগাওয়াটের বেশি। তবে সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে অবসরে যাবে প্রায় চার হাজার মেগাওয়াট সক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্র। সেক্ষেত্রে ২০২৭ সালের মধ্যে দেশে বিদ্যুৎ খাতের মোট উৎপাদন সক্ষমতা দাঁড়াবে ৩৭ হাজার মেগাওয়াটের কিছু বেশিতে। (বণিক বার্তা, ১১ মার্চ, ২০২৩)
হাসিনা সরকার ২০১০ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনে মহাপরিকল্পনা নেয়। সেই প্রাক্কলিত কেন্দ্রগুলোর হিসাব ধরেই আমরা ২০২৭ সাল নাগাদ পাবো ৩৭ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। কিন্তু ওই বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্র তৈরিতে যে শিল্পায়নের আয়োজন করেছেন সরকার, তা অনেকটাই হতাশাজনক।
এই হতাশা প্রকাশ করেছে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। যেমন ২০২৩ সালের আগেই আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২৫-৫৬ হাজার ৭০০ মেগাওয়াট থাকলেও সর্বোচ্চ ১৩ হাজার মেগাওয়াটের চেয়ে বেশি নেই চাহিদা। তাহলে বাকি ১৩ হাজার মেগাওয়াট তো উৎপাদনই করতে পারছে না কেন্দ্রগুলো। তার ওপর গ্যাস, ফার্নেসঅয়েল কেনার জন্য যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দরকার, সরকার তা ব্যয় করতে পারছে না। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে সামনের দিনগুলোর কথা ভেবে সরকার খাদ্য কেনার অর্থ রেখে সাশ্রয়ী নীতিতে এগোচ্ছে।
এই সাশ্রয়ী পদ্ধতির ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন সেক্টরে যে কুপ্রভাব পড়ছে, তা যে জিডিপিতে আঘাত হানবে, তা কি সরকার লক্ষ্য রাখেননি। এই সময়েই শিল্প সেক্টরে জ্বালানি সংকটের কারণে অনেক কারখানাই বন্ধ হয়ে গেছে ছাঁটাই হয়েছে শত মত বা হাজার হাজার শ্রমিক। গার্মেন্টসের দশা আরও খারাপ ফ্রান্স ও জার্মানির ওয়ার্কঅর্ডার মাত্র ২০ শতাংশ কমেছে।
ভারত থেকে না অয়েল না গম কোনোটাই আসবে না। গমের জন্য আমাদের উন্মুখ হয়ে থাকতে হবে ইউক্রেনের দিকে। সেখানে রাশিয়ার দয়া হলে ছেড়ে দিতে পারে ওডেসা বন্দর থেকে আরও দুটি বন্দর গম রফতানির জন্য। আবার রাশিয়া থেকেও আমরা বা বিশ্বের অপরাপর দেশ গম কিনতে পারছে না, মার্কিনি নিষেধাজ্ঞার কারণে।
এ এক জটিল ও অমানবিক বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে আমাদের কি করা উচিত, সেই পথের সন্ধান করা জরুরি। বন্ধু দেশ আমেরিকা, স্ট্রাটেজিক্যালি বাংলাদেশকে তার বগলের নিচে রাখতে চাইলেও তার গম থেকে জ্বালানি তেল উৎপাদন বাদ দিয়ে তা গরিব দেশের মানুষের কাছে বিক্রি করবে, এমন সহজ সমাধানে পৌঁছার সময় এটা নয়। আর বাংলাদেশ তো এখন আরেকটি রাজনৈতিক ফাঁদের নালায় পা দিয়ে বসে আছে।
২০২৬ সালে আমরা মধ্যম আয়ের দেশের বহরে ঢুকে যাচ্ছি। আমাদের অর্থবিত্ত শনৈ শনৈ বাড়ছে। আমরা তো খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ! এই দাবি সত্য হোক, এটা আমরা চাই কিন্তু আমাদের পেঁয়াজ-রসুনের ঘাটতির চেয়েও শস্য ঘাটতি কিন্তু মোটেও কম নয়। প্রতি বছর বাংলাদেশ কেবল ইউক্রেন থেকেই গম আমদানি করে ৬.০৪ লাখ টন।
এর জন্য কত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হচ্ছে, তা একবার হিসাব করে দেখুন। ৩৭ টাকা কেজি দরে আনছি আমরা ইউক্রেনের গম। এই হিসাব আমাদের সরকারের রাজস্ব বোর্ডের। আমরা এটা ভুলে যাইনি যে আমাদের জনসংখ্যা এখন ১৭ কোটিরও বেশি। এই এতো মানুষের বসবাসের জায়গা দিতে গিয়ে কমেছে চাষের আবাদের জায়গা। তার ওপর গোদের ওপর ফোড়া হিসেবে আছে রোহিঙ্গারা।
এদের জায়গা দিতে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের কক্সবাজারের বিপুল পরিমাণ ভূমি যেমন গেছে, তেমনি গোটা এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস হতে চলেছে। সেই সঙ্গে রোহিঙ্গানটোরিয়াসদের হিংস্রতা এতোটাই উন্মত্ত যে তারা খুটোখুনির পাশাপাশি মাদক ও সোনা এবং অস্ত্র চোরাচালানে জড়িয়ে পড়েছে। ওই এলাকার জীববৈচিত্র্য তো ধ্বংস হচ্ছেই, সেই সঙ্গে আমাদের রাজনীতিতে লেগেছে এর কুপ্রভাব।
সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য যে লাইন তৈরিতে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের সমন্বিত পরিকল্পনা না থাকায়ই এমন ভারসাম্যহীনতা বিরাজ করছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়িয়ে কোনোই লাভ হবে না, যদি ব্যবহার ক্ষেত্র ও তা সঞ্চালন ও বিতরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা না হয়।
শিল্পাঞ্চল, শিল্পজোন ও বিদেশি বিনিয়োগের জোন নির্মাণ সম্পন্ন করতে হবে সমান্তরালে। এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ায় আমাদের বিদ্যুতের মেগা উৎপাদন বিফলে যাবে। এই বিষয়গুলো মনে রেখে সরকারকে এগোনোর কথা বলছি আমরা। আর যাই হোক, অদক্ষ রাজনৈতিক আমলা দিয়ে টাকা খরচ হবে, কাজের কাজ হবে না।
লেখক: কবি, সাংবাদিক।
এইচআর/ফারুক/এমএস