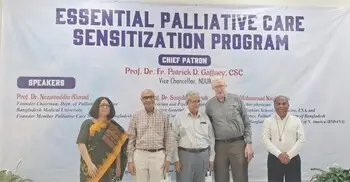ক্রীতদাসের হাসি: তাতারীর আর্তনাদ

কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানের আসল নাম ‘শেখ আজিজুর রহমান’। তবে তিনি শওকত ওসমান নামেই লিখতেন। ‘ক্রীতদাসের হাসি’ তাঁর লেখা বিখ্যাত উপন্যাস। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘জননী’ও পাঠকসমাজে সমাদৃত। ‘ক্রীতদাসের হাসি’ তাঁর তৃতীয় উপন্যাস। ১৯৬১ সালে রচিত উপন্যাসটি প্রথম ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়।
১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসন পাকিস্তানকে বর্বর স্বৈরশাসনের যাঁতাকলে আবদ্ধ করে। এ সময় সব ধরনের বাক-স্বাধীনতা হরণ করা হয়। তৎকালীন পাকিস্তানের স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের শাসন ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করে এ উপন্যাস রচিত হয়।
উপন্যাসের মূল চরিত্র তাতারী। গণতান্ত্রিক চেতনাকে ভয় পায় স্বৈরাচারী শাসক। এ চেতনাকে দমন করার জন্যই আবার নেমে আসে সামরিক শাসন। তবুও লেখকের প্রতিবাদ স্তব্ধ থাকেনি। রূপকের মধ্য দিয়ে তীব্র হয়ে উঠেছে এ প্রতিবাদ। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে শওকত ওসমানের ‘ক্রীতদাসের হাসি’র তাতারী। খলিফা হারুনর রশীদ কোনো কিছুর বিনিময়েই তাতারীর হাসি শুনতে পান না। খলিফার নির্দেশে হাসার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করেন তাতারী।
উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয় হাবশি গোলাম তাতারী আর বাদী মেহেরজানের প্রেমময় হৃদয় উৎসারিত হাস্যকলরোলের মধ্য দিয়ে। লেখক বলছেন, ‘দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে। বান্দা কেনা সম্ভব-! কিন্তু-কিন্তু-ক্রীতদাসের হাসি-না-না-না-না-।’ ক্রীতদাসের হাসির মূলভাব তুলে ধরতে উপন্যাসের অন্তিম মুহূর্তে ক্রীতদাস তাতারীর এ আর্তনাদটুকুই যথেষ্ট।
রাজমহলের অদূরে স্ত্রীর সঙ্গে ক্রীতদাস তাতারীর উদ্দাম সুখ-হাসি চঞ্চল করে তোলে সম্রাট হারুনকে। অধরা সেই হাসিকে বারবার শুনতে এবং নিজের করে নিতে ক্রীতদাস তাতারীকে নিজের ধন-সম্পদের প্রাচুর্যবলয়ে বন্দি করেন। দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ বাদশাহ হারুনর রশীদ হাবশি গোলাম তাতারীর হাসি শুনে ভয়ানক ঈর্ষান্বিত হন।
শৃঙ্খলের আদলে বন্দি তাতারী হাসতে ভুলে যান। আনন্দের সীমানায় ভাসার স্রোত হারিয়ে ফেলেন। এমনকি সম্রাটের প্রবল হুকুমেও সেই অমৃত সুখ-হাসি আর জাগ্রত হয়ে ওঠে না। বাদশাহের সুকৌশলী নির্যাতনের খড়্গ নেমে আসে তাতারী আর মেহেরজানের ওপর।
খলিফা হারুনর রশীদ কোনো কিছুর বিনিময়েই তাতারীর হাসি শুনতে পান না। ফলাফল ক্রুদ্ধ খলিফার নির্দেশে তাতারীর বিচ্ছিন্ন গর্দান মাটিতে পড়ে যায়। খলিফার নির্দেশে হাসার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করেন তাতারী। উপন্যাসের শুরু, শেষ ও মাঝের ছত্রে ছত্রে নাটকীয়তার তীক্ষ বাঁক পাঠককে চমকে দেবে।
শাসন-শোষণে পূর্ববাংলার জনগণের মৌলিক চাহিদা থেকে শুরু করে জীবনের স্বপ্ন যেমন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কবজা করে রেখেছিল। উপন্যাসেও দেখা যায়, খলিফা চরিত্র প্রলেতারিয়েত বা নিম্নবর্গীয় শ্রেণি ‘ভৃত্য তাতারী’কে আড়ষ্ট এবং দাবায়ে রাখতে চেয়েছিল। কবজা করে রাখতে চেয়েছিল তার মৌলিক চাহিদাসম্পন্ন স্বপ্ন বাস্তবতাগুলোকে।
১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠী যেমন বাঙালির মা-বোনদের সম্ভ্রমের ওপর তাণ্ডব চালিয়েছিল। এখানেও খলিফা হারুন তার কর্মচারী তাতারীকে বন্দি এবং নির্যাতনের মাধ্যমে তারই পরমা সুন্দরী স্ত্রীকে ভোগ ও সম্ভ্রমহানির সেই তাণ্ডব চালিয়েছেন।
১৯৬২ সালে বসেই ঔপন্যাসিক ১৯৭১ সালে ঘটতে যাওয়া পূর্ববাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের চরিত্র বুঝে ফেলেছিলেন! যাকে ইঙ্গিত হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন তার উপন্যাসের ক্যানভাসে। লেখক তার দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে সমাজব্যবস্থার শোষণকে ‘ক্রীতদাসের হাসি’ উপন্যাসের মাধ্যমে রূপকার্থে প্রকাশ করেছেন।
শওকত ওসমান ১৯৯৫ সালে ‘পুঁথিঘর লিমিটেড’ থেকে পুনরায় প্রকাশ হওয়ার পর ভূমিকায় লিখেছিলেন, ‘জুয়াড়ির মতো আমি দান ধরেছিলাম। হয় জয়, অথবা সর্বনাশ সুনিশ্চিত। জিতে গিয়েছিলাম শাসক শ্রেণীর মূর্খতার জন্যে। বছরের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের পুরস্কার পায় ক্রীতদাসের হাসি।’ বইটি ১৯৬৬ সালে ‘আদমজী সাহিত্য পুরস্কার’ লাভ করে।
শওকত ওসমানের ‘ক্রীতদাসের হাসি’ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন কবীর চৌধুরী। নাম রাখেন ‘দ্য লাফটার অব এ স্লেভ’। উপন্যাসটি সংলাপ নির্ভর রূপক উপন্যাস। তবে এটি আসলে কী—উপন্যাস নাকি নাটক? সর্বত্র একে উপন্যাস বলে উল্লেখ করলেও এর গঠন প্রায় নাটকের মতোই।
এসইউ/জেআইএম